 |
| সত্যজিৎ রায় |
সত্যজিৎ রায়। বাংলার শ্রেষ্ঠ মানুষদের কাতারে যখন কিংবদন্তীর নামোল্লেখ করার সময় হয় তখন এই নামটা না নিলে সেই লিস্ট বাতিল বলে গণ্য হবে প্রায় অধিকাংশ বাঙালির কাছে। ১৯২১ সালে দোসরা মে এই কিংবদন্তীর জন্ম হয় তৎকালীন বিখ্যাত এক বংশে কিন্তু সেই বিখ্যাত বংশের যশের কারণে তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় উঠে আসেনি। তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনার বিকাশ এতটাই প্রখর ছিল যে বলা যায় তাঁর পিতামহ বা পিতার পরিচয়ও খানিকটা তাঁর মাধ্যমে হয়েছে। বলা যায় রায় পরিবার তখন কলকাতার সম্ভ্রম এবং বিখ্যাত পরিবারদের একটি। পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর এবং পিতা সুকুমারকে তখন সাহিত্য জগতের এক অনন্য তারা বলে মানা হতো। তাই বলে বলা যায় না সত্যজিৎ রায় তাঁর পিতৃ পরিচয়ে যশের তুঙ্গে এসেছেন।
তাঁর পিতা এবং পিতামহ দুজনেই ছিলেন শুধু সাহিত্যের নক্ষত্র অপরদিকে সত্যজিৎ ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, সঙ্গীত পরিচালক, লিপিকলাবিদ, অঙ্কনশিল্পী ইত্যাদি।
অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিষয়ে তার মাধুর্য তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন। যেখানেই হাত বুলিয়েছেন সেখানে সোনা ঝড়েছে। বাংলা সাহিত্য বা চলচ্চিত্রের এক আমূল পরিবর্তন তিনি যে এনেছিলেন তা এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও অস্বীকার করা যায় না। তাঁর বানানো ফিল্মগুলো এখনও বাঙালির মনে দোলা দিয়ে ওঠে। হয় নিত্যনতুন আঙ্গিকে রিমেক। আজ সেই কিংবদন্তীর সৃষ্ট কিছু চরিত্র নিয়ে আলোচনা করবো। যেমনটা তিনি নিজে বিখ্যাত হয়েছেন নিজের কাজের মাধ্যমে ঠিক তেমনটাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোও বিখ্যাত হয়েছে তাদের কাজের মাধ্যমে।
সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্ট চরিত্র এতই বেশি যে তাঁর প্রত্যেকটা সৃষ্টি নিয়ে কথা বলতে গেলে শব্দের ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে। তাই টার্নিং পয়েন্টের চরিত্র নিয়েই বেশি আলোচনা করবো তবে মজার বিষয় হচ্ছে সত্যজিৎ রায় তার সৃষ্ট চরিত্র দিয়েও একেকটা চরিত্র সৃষ্টি করতেন। তার সৃষ্ট চরিত্রদের নিয়ে কথা বলতে হলে তাদেরকে দুটো ভাগে ভাগ করতে হয়। এক. সাহিত্যজগতের চরিত্র দুই. চলচ্চিত্র জগতের চরিত্র। তবে আজকে সাহিত্যজগতের চরিত্রদের নিয়ে আলোচনা করবো।
• সাহিত্যজগতে সৃষ্ট চরিত্রসমূহ:
ফেলুদা:
প্রথমেই যে চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ করবো তার নাম ফেলুদা। এই নামটার সাথে অপরিচিত আছে এমন বাঙালি বইপড়ুয়া খুব কম আছে পৃথিবীতে। বইপড়ুয়া ছাড়ুন যে লোক জীবনে দুদণ্ড বই ছুঁয়ে দেখনি তিনিও হয়তো বলে দেবেন ফেলুদার কথা। ফেলুদা চরিত্রটি সত্যজিৎ রায় যে খুব পরিকল্পনা করে পাঠকের সামনে এনেছিলেন এমন না। ধরতে গেলে একদম তাৎক্ষণিকভাবে একটা ক্যারেক্টার তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন সে সময়।
বলছি ১৯৬৫ সালের কথা। কোনো রকম খসড়া ছাড়াই একটা চরিত্রকে সৃষ্টি করেন সত্যজিৎ রায়৷ এ নিয়ে সন্দীপ রায় বলেন, "এক নতুন চরিত্র জন্মের আগে, একজন লেখক সাধারণত যেসব প্রাথমিক খসড়া করে থাকেন, উনি তা কিছুই করেননি। গত চার বছরে লেখা অন্যান্য গল্পের মতো সরাসরি আরম্ভ করে দিয়েছেন।"
অর্থাৎ ফেলুদার আবির্ভাব খুব সাধারণ ভাবেই হয়েছিল। সত্যজিৎ রায়ের কিছু নোটখাতা ছিল যাতে তিনি বিভিন্ন গল্পের খসড়া টুকে রাখতেন কিন্তু ১৯৬৫ সালের আগে তাঁর সেই সব খাতায় ফেলুদার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। হঠাৎ করে ১৯৬৫ সালে তার বিখ্যাত লাল রঙের খসড়া খাতার তৃতীয় পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় ফেলুদার নাম।
১৯৬৫ সালে সন্দেশ পত্রিকায় প্রথম ফেলুদাকে নিয়ে লেখেন সত্যজিৎ রায়। গল্পের নাম ছিল ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি। ফেলুদার আসল নাম প্রদোষ চন্দ্র মিত্র। তবে অধিকাংশ লোক তাকে ফেলু মিত্তির বলেই চেনেন।
কলকাতার রজনীসেন রোডে কাকার বাড়িতেই ফেলুদা থাকতেন। খুড়তুতো ভাই তপেশকে সাথে করে চড়িয়ে বেড়াতেন বিভিন্ন জায়গায়। প্রথম গল্পতেই পাঠকদের কাছে জমে যায় ফেলুদা। এরপরে বেশ কিছু বছর পর পাঠকের চাহিদার জের ধরে সত্যজিৎ রায় লেখেন বাদশাহী আংটি। এরপর আর থেমে থাকেনি ফেলুদার গল্প। ১৯৬৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ক্রমিক আকারে নয়তো সংকলন আকারে ফেলুদার আবির্ভাব হয়। ছোটো বড়ো মিলিয়ে প্রায় ৩৫ টা সম্পূর্ণ এবং ৪ টা অসম্পূর্ণ গল্প ও উপন্যাস লিখে যেতে পেরেছেন সত্যজিৎ রায়৷ এবং তা নিয়েই রচিত হয়েছে বিখ্যাত ফেলুদা সিরিজ বা সমগ্র।
ফেলুদার চরিত্রটি ছিল বাঙালি ডিটেক্টিভ। শুধু ডিটেক্টিভ বললে ভুল হবে। রহস্যের পাশাপাশি ফেলুদার গল্পে ছিল একেকটা ভ্রমণের কারুকার্য। তাঁর রচিত বেশ গল্পেই তিনি এ ধাঁচটা রেখেছেন। এর কারণ ছিল সত্যজিৎ বেশ ভ্রমণবিলাসী ছিলেন এবং সেই ধারাটা তিনি ফেলুদার গল্পে ছড়িয়ে দিতেন। মূলত ফেলুদাকে সৃষ্টির পেছনে অনেকে মনে করেন যে শার্লক হোমস থেকে প্রভাবিত হয়ে সত্যজিৎ ফেলুদাকে সৃষ্টি করেছেন। শার্লকের যেমন একজন সহকারী রয়েছে এবং তার মাধ্যমে রহস্যের বর্ণনা বর্ণিত হয় ঠিক তেমন ফেলুদারও সহকারী তোপসের মাধ্যমে গল্প বা উপন্যাস বর্ণিত হতে দেখে অনেকে ফেলুদাকে বাঙালি শার্লক বলেও আখ্যা দিয়েছিলেন।
ফেলুদা বয়সে ছিল ২৭ বছরের তরুণ। যার উচ্চতা ছিল ৬.২"। ফেলুদার জ্ঞানের পরিধি ছিল প্রগাঢ়। সে তার এই জ্ঞানের পরিধি এবং পর্যবেক্ষণের বিষয়টাকে মজা করে বলতো মগজাস্ত্র। ফেলুদার সাথে একটা রিভলবার থাকলেও খুব কম সংখ্যক গল্পে সেই রিভলবার চালানোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মূলত ফেলুদার মার্শাল আর্টের দক্ষতাটাকেই সত্যজিৎ বেশি করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।
ফেলুদার নয় বছর বয়সে বাবা মা মারা যায়। এরপরে বাবার ছোটোভাইয়ের কাছেই ফেলুদা বড়ো হয়ে ওঠে। ফেলুদার জীবনাচরণে জানা যায় ফেলুদার বাবা জয়কৃষ্ণ মিত্র ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে গণিত ও সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন।
ফেলুদার ইতিহাস এবং ভূগলের দখলও ছিল অনেক। তার গল্পের বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থানের ব্যাখ্যা বেশ সুনিপুণ ভাবে সত্যজিৎ দিয়েছে যাতে বোঝা যায় ফেলুদার ভূগোলের দখল কতটুকু! এছাড়াও ফেলুদার চারমিনার সিগারেট খাওয়ার জন্যে কত কিশোর যে সিগারেট ধরেছিল তা বলাই বাহুল্য!
ফেলুদাকে বইয়ের পাতায় ফোটানো ছাড়াও চলচ্চিত্রেও ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যজিৎ রায়। সে সময়ের বিখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে ফেলুদার রোল করানোও ছিল তার করা অন্যতম একটি কাজ। এরজন্য প্রায় গল্পের অঙ্কনে ফেলুদার ভেতর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা আঁচ ছিল। এবং অনেকেই মনে করতেন সে সময়ে যে ফেলুদার ক্যারেক্টারটা যেন সৌমিত্রকেই কেন্দ্র করে সাজিয়েছিলেন সত্যজিৎ।
সত্যজিৎ জীবিত থাকতে ফেলুদার গল্পে দুটো চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। আর দুটোতেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছিল ফেলু চরিত্রে। সোনার কেল্লা এবং জয় বাবা ফেলুনাথে অভিনয়ের পর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়েরও ফেলুদা ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল। এরপর সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ রায়ের পরিচালনায় বেশ কিছু চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল ফেলুদাকে নিয়ে যার অধিকাংশতেই সব্যসাচী ছিলেন ফেলুদার ভূমিকায়।
আমার সাথে ফেলুদার পরিচয় ২০১২ এর পরে। তখন স্কুলের লাইব্রেরিতে একটা ম্যাগাজিন আসতো। মনে আছে সেই ম্যাগাজিনে ফেলুদাকে নিয়ে একটা বিশ্লেষণধর্মী আর্টিকেল ছিল। খুব ছোটো ছিল আর্টিকেলটা। সেখানে ফেলুদার গোয়েন্দার কথা জানতে পাই। এরপর ধীরে ধীরে আনন্দ পাবলিশার্সের পাইরেট কপি সংগ্রহ করা শুরু করি। ২০১৪ সালে আবীর চট্টোপাধ্যায় অভিনীত বাদশাহী আংটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেলে সেটা দেখি। ব্যস এরপর ফেলুদা হয়ে ওঠে আমার দ্বিতীয় পারফেক্ট গোয়েন্দা। প্রথমজন শার্লক বাবু ছিলেন।
২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আমি ফেলুদার প্রায় দুটো খণ্ডই শেষ করি। যতটা পড়তাম ফেলুদার রহস্য উদঘাটনের জন্য তার থেকেও বেশি পড়তাম ভ্রমণকাহিনীর জন্য। ফেলুদার প্রায় প্রত্যেকটা গল্পই একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থেমে থাকেনি। এদিক সেদিক ক্লু এর জন্য যেতে হয়েছেই। যারা পড়েছেন তারা ভালো করে জানবেন এই বিষয়টা।
তপেশরঞ্জন মিত্র:
ফেলুদার চরিত্রের কথা টানতে গেলে অন্যান্য যত চরিত্রের কথা উল্লেখ করতে হয় তার মধ্যে তপেশরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসেকে প্রথমে টানতে হয়। সম্পর্কে ফেলুদার খুড়তুতো ভাই হলেও মূলত সত্যজিৎ রায় এই চরিত্রটাকে ফেলুদার সেকেন্ড পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করেছে।
গোয়েন্দা কাহিনিতে সহকারী ক্যারেক্টার থাকা বাঞ্চনীয়। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল থেকে শুরু করে শরদিন্দুর ব্যোমকেশ অব্দি একজন সহকারী রয়েছে বলেই দেখা যায়। অর্থাৎ যে হত্যাকাণ্ড বা মূল চরিত্রের পদক্ষেপগুলো রচনা করবে। সত্যজিৎ রায় তপেশকে দিয়ে ঠিক এই কাজটাই করিয়েছিলেন। অর্থাৎ ফেলুদার সব ডিটেইলস তপেশ লিখতো। যার মাধ্যমেই ফেলুদার সকল কিছু জানতে পারতো পাঠক।
বলা হয় সত্যজিৎ রায় শার্লক হোমসের সহকারী ডাঃ ওয়াটসনের আঙ্গিকে তপেশ ওরফে তোপসেকে সৃষ্টি করেছেন।
তোপসের চরিত্রটি বলতে গেলে একটা কিশোর চরিত্র। তপেশের বয়স জানা যায় ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি গল্পে৷ সাড়ে তেরো বছর তথা ফেলুদার বয়সের অর্ধেক। যদিও এ নিয়ে বেশ কিছু গল্পে ফেলুদা টিজ করেছিল তপেশকে।
সত্যজিৎ রায় তপেশকে স্মার্ট, কিশোর রোমাঞ্চকর একটা ভাইব দিয়েছেন। যাতে কিশোর কিশোরীরা ফেলুদা পড়ার সময় যেন পড়তে কষ্ট না হয়। সত্যজিৎ রায় বুঝেছিলেন শার্লক হোমস সবাই পড়লেও কিশোর বা কিশোরীরা ওদিকে তেমন আগায় না। আর এর জন্যেই তিনি ফেলুদার গল্পে একজন কিশোর রহস্য রোমাঞ্চকর ক্যারেক্টার তপেশকে রেখেছেন।
তপেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জানা যায় সে লম্ভা, সুদর্শন, উজ্জ্বল রঙের চেহারা তার।
তপেশের পড়াশোনা নিয়ে তেমন জানা যায় না। তবে সোনার কেল্লা বইতে তপেশের মা কে বেশ ক'বার তার ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করতে দেখা গেছে। এছাড়াও কৈলাশে কেলেঙ্কারি উপন্যাসে উল্লেখ পাওয়া যায় তার মেট্রিক পাশের কথা।
ফেলুদার মতো তপেশেরও বই পড়ার নেশা ছিল। জ্ঞান বাড়ানোর জন্য প্রচুর বই পড়তো। আর এই জ্ঞান পরখ করতো খোদ ফেলুদা নিজেই। তার এই জ্ঞানের কারণে ফেলুদার উপন্যাসে তাকে বেশ সক্রিয়ভাবে দেখা যায়।
ফেলুদার অবর্তমানে বেশ কিছু শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সামাল দিতে দেখা যায় তপেশকে।
লালমোহন গাঙ্গুলি:
লালমোহন গাঙ্গুলি চরিত্রটি সত্যজিৎ রায় টেনেছিলেন ফেলুদার গল্পে যাতে রহস্যের বেড়াজালে লোকে মেজমেজে হয়ে না ওঠে বরং হাসি খুশি থাকে সেই বিষয়টা নিশ্চিত করতে। যাকে কমিক রিলিফও বলা যায়। যারা পাঠক আছেন ফেলুদার তারা লক্ষ করে দেখবেন বেশ কিছু দীর্ঘ তদন্তে লালমোহন গাঙ্গুলি চরিত্রটার প্রভাব বেশ করে রেখেছিলেন সত্যজিৎ রায়।
লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গেলে দেখা যায় মাঝ বয়সী একটা লোক, মাথায় টাক রয়েছে, নাকের নিচে রয়েছে গোঁফ, পরনে সবসময় ধুতি পাঞ্জাবি, রসিকতা করতে পছন্দ করেন, সিগারেট ছাড়েন আবার ধরেন, চপ্পল পরিধান করেন এবং এ নিয়ে সবাইকে উপদেশ দিতে ভোলেন না।
উপন্যাসে লালমোহন গাঙ্গুলি একজন রহস্য ঔপন্যাসিক। তার গল্পের মেইন ক্যারেক্টারের এত এত গুণ তিনি দিয়েছিলেন যে সেই গুণের কারণে ফেলুদাকেও বেশ উপহাস করতে দেখা গেছে। এছাড়াও তার উপন্যাসে হাস্যরসের উপস্থিতি দেখে প্রায়ই ফেলুদা খোঁচা মারতো। তার ওপর বিভিন্ন ধরনের ভুল ধরিয়ে দিতেও দ্বিধা করতো না।
ফেলুদার গল্পে জটায়ুর প্রথম আগমন সোনার কেল্লা উপন্যাসে৷ প্রশ্ন আসতে পারে যে এরকম একটা ক্যারেক্টারের আগমন কেন এত দেরিতে আনলেন সত্যজিৎ? এর কয়েকটা কারণ ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল তখনকার সময়ের অন্যান্য গোয়েন্দা ঔপন্যাসিকদেরকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া।
একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন ফেলুদার গল্পে জটায়ুর ভূমিকা ছিল তার নিজস্ব লেখালেখির বড়াই করা আর ফেলুদার মাধ্যমে তা ধূলিসাৎ হওয়া। বিভিন্ন জটিল এবং বিবিধ বিষয়কে তিনি না বোঝার ভান ধরে প্রশ্নবাণে জড়িয়ে দিয়েছেন। এটার আরেকটা ফর্ম হিসেবে ধরা যায় রিফ্লেক্সিবিলিটি। তখনকার সময়ে হেমেন্দ্র কুমার, দস্যুমোহন ন্যায় লেখকরা তাদের গল্পে মূল চরিত্রকে এতটাই বড়ো করেছিলেন যে তাদেরকে দেবতুল্যভাবে তৈরি করতেন প্রত্যেকটা গল্পে। যে কি না তুখোড় জ্ঞানী এবং অভাবনীয় শক্তিশালী। যেমনটা প্রখর রুদ্রের মাধ্যমে সত্যজিৎও করেছেন। অর্থাৎ সত্যজিতের ব্যঙ্গধর্মী জ্ঞান কতটুকু প্রখর তা এই জটায়ু ক্যারেক্টারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যায়। সত্যজিৎ তাঁর গল্পেই একটা কাল্পনিক লেখক রেখে সেই লেখার চরিত্রকে প্রশ্ন করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে জটায়ু ছিল প্রত্যেকটা গল্পের কাউন্টার পয়েন্ট। সমালোচনা, সস্তা ট্রেডিশনকে ধুয়ে দেওয়া ইত্যাদি সবকিছু জটায়ুকে দিয়ে করিয়েছেন সত্যজিৎ।
২০২০ সালে শুভদীপ অধিকারীর লেখা 'জয়তু জটায়ু' বইতে জটায়ু সম্পর্কে সুবিন্যস্ত আলোচনা করা হয়েছে।
মগনলাল মেঘরাজ:
ফেলুদার উপন্যাসে যদি কোনো খলনায়কের কথা উল্লেখ করতে হয় তবে সবচেয়ে ভয়ানক হবে মগনলাল মেঘরাজ। তিনটি উপন্যাসে তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। জয় বাবা ফেলুনাথ, যত কাণ্ড কাঠমুন্ডুতে এবং গোলাপী মুক্ত রহস্যে। বলা হয় এই চরিত্রটাও সত্যজিৎ টেনেছিলেন শার্লক হোমসের বিখ্যাত খলনায়ক প্রফেসর মরিয়ার্টির ছন্দ রেখে।
তবে ফেলুদার উপন্যাসে খলনায়ক হিসেবে সবচেয়ে সক্রিয় দেখা গেছে মগনলালকে। মগনলাল থাকলে ফেলুদা যেন আরও তৎপর হয়ে ওঠে রহস্য উদ্ধারের জন্য। বলা যায় ফেলুদার চরম শত্রু মগনলাল।
মগনলালের বসবাস বেনারসে৷ এছাড়াও কলকাতায় তার বাড়ি রয়েছে। তার একটা ছেলেও রয়েছে নাম সুরুজলাল।
জয় বাবা ফেলুনাথে মগনলালের ভূমিকা ছিল গয়না পাচারে। এরকমই গণেশ মূর্তি পাচারের সময় ফেলুদা তাকে হাতেনাতে ধরেছিল।
ফেলুদা সিরিজের উনিশতম বই যত কাণ্ড কাঠমুন্ডুতে ফেলুদা যখন দেখে যে মগনলাল জেলের বাইরে তখন সে অবাক হয় না। এরপরে যত কাণ্ড কাঠমুন্ডুতেও তাকে চোরাচালান আর হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়।
কিন্তু সেটাও তার বড়ো শাস্তি ছিল না কারণ সিরিজের চল্লিশতম বই গোলাপী মুক্ত উপন্যাসেও দেখা যায়।
সিধু জ্যাঠা:
পুরো নাম সিদ্ধেশ্বর বোস। ফেলুদার গল্পে ফেলুদার বাবার বন্ধু হিসেবে এর আগমন হয়। সম্পর্কে এর জন্য ফেলুদা জ্যাঠা হিসেবে মানতো তাকে। ইতিহাসে বেশ পটু ছিলেন তিনি।
ফেলুদার গল্পে তথ্যের অভাব পড়লেই তার কাছে ফেলুদা ছুটে আসে। যত রকমের নিউজের তথ্য রয়েছে তা সংগ্রহ করে রাখতেন তিনি। দিন পঞ্জিকার জ্ঞানেও অগাধ পাণ্ডিত্যের দর্শন পাওয়া যায় তার চরিত্রে।
প্রত্যেকটা গোয়েন্দা চরিত্রের একটা তথ্যভাণ্ডার দরকার পড়ে৷ সত্যজিৎ রায় ফেলুদার গল্পে সিধু জ্যাঠার চরিত্রটা ঠিক সেই রূপেই গড়েছিলেন। সব কাহিনীতে তার উপস্থিতি না থাকলেও বেশ কিছু গল্পে তার ভূমিকা ছিল বেশ প্রগাঢ়।
আলোচিত হয়েছে যে সিধু জ্যাঠা চরিত্রটি বাস্তবেই ছিল এবং সত্যজিতের সাথে পরিচয় ছিল। অর্থাৎ সত্যজিতের পরিচয়ে এমন একজন লোক ছিল যে কি না পচুর তথ্য আর বই সংগ্রহ করতো। পরবর্তীতে সেই কনসেপ্টটাকে সিধু জ্যাঠায় ট্রান্সফার করেছে সত্যজিৎ।
হরিপদ দত্ত:
এই চরিত্রটা মূলত কিছু গল্পে ফেলুদাদের সাহায্য করতো। যেমন গোরস্থানে সাবধান গল্পে একবার লালমোহন গাঙ্গুলি, তপেশ, ফেলুদা তিনজনের জীবন বাঁচিয়েছিল সে। এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করতো লালমোহন গাঙ্গুলিকে৷
পুলক ঘোষাল:
কাহিনীতে একজন মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র পরিচালক ঘোষাল। তবে থাকে কলকাতায়। লালমোহন বাবু যেখানে থাকেন সেই পাড়ায় তার বসবাস তথা উত্তর কলকাতায়। লালমোহন বাবুর গল্প নিয়ে সিনেমা তৈরির সময় বেশ বিপজ্জনক ঘটনা ঘটেছিল। বোম্বাইয়ের বোম্বেতে এই কাহিনির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ফেলুদার কারণে সেই ছবির প্রডিউসার গ্রেপ্তার হয় আর দার্জিলিং জমজমাটে অভিনেতা। সেই থেকেই ফেলুদার সাথে পরিচয়।
বৈকুন্ঠ মল্লিক:
এই চরিত্রটির সরাসরি কোনো ভূমিকা না থাকলেও জটায়ুর মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে এর ভূমিকা রয়েছে। পরিচয়ে তিনি জটায়ুর শিক্ষক। সপ্তম শ্রেনিতে পড়ার সময় এই শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসে জটায়ু। তার মতে দারুণ এক কবি ছিলেন বৈকুন্ঠ মল্লিক। আর এর দরুন বেশ কিছু কাহিনিতে জটায়ুকে তার কবিতার আবৃত্তি করতে দেখা গিয়েছে।
প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু:
সাল ১৯৬১। নিজ পারিবারিক পত্রিকা সন্দেশের তৃতীয় সংস্করণ বের করার সময় কিছু গল্পের দরকার হয়। কোনো রকম পরিকল্পনা ছাড়াই সত্যজিৎ একটা গল্প দেন। নাম ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি। ১৯৬১ সালের সন্দেশের আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এর তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় গল্পটি। সেই সূচনা থেকে বাঙালি পাঠক সমাজ পায় প্রোফেসর চ্যালেঞ্জারের মতো এক বিজ্ঞানী। শুধু বিজ্ঞানী বললে ভুল হবে। প্রোফেসর শঙ্কু ছিলেন একজন অভিযাত্রী।
শঙ্কুর প্রসঙ্গে সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ বলেন, "তিনি (সত্যজিৎ) প্রচুর ভ্রমণ করতেন। সবজায়গায় যেতেন আর যেখানে যেতে পারতেন না সেখানে তিনি শঙ্কুকে পাঠাতেন।"
প্রোফেসর শঙ্কুর সৃষ্টির পেছনে পত্রিকার খাতা ভরাট করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কারণ তখনও সত্যজিতের কাছে ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বলেছিলেন যে বাবা সুকুমার রায়ের হেসোরাম হুঁশিয়ারি-র ডায়েরি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রোফেসর শঙ্কুকে তৈরি করেছিলেন। এই চরিত্রটার জন্যেও সত্যজিৎ কোনো আগাম ধারণা রাখেননি।
প্রোফেসর শঙ্কুর চরিত্রটি এতটাই বিস্তৃত যে এ নিয়ে বিশদ আকারে আলোচনা করা যাবে এবং তাতে প্রচুর শব্দের দরকার হবে। তাই প্রসঙ্গক্রমে যতটুকু না জানলেই নয় ততটুকুর আলোচনা করছি।
প্রোফেসর শঙ্কু ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, অভিযাত্রী ও গবেষক। তিনি ৬৯টি ভাষায় পারদর্শী, ৭২টি আবিষ্কারের আবিষ্কারক। হায়রোগ্লিফিক, মহেঞ্জোদারো, হরোপ্পার মতো কঠিন ভাষা ও লিপি উদ্ধার করায় সক্ষম।
তিনি দারুণ অভিযাত্রীও বটে। এ দেশ থেকে ও দেশ এমনকি মঙ্গলেও তার পদচারণা রয়েছে।
অধুনা ঝাড়খণ্ডের গিরিডিতে প্রোফেসর শঙ্কুর বসবাস। পিতা শ্রী ত্রিপুরেশ্বর একজন আয়ুর্বেদিক। বাবা শঙ্কুকে তিলু বলে ডাকতেন। প্রোফেসর শঙ্কুর ভাণ্ডারে বেশ কিছু সার্টিফিকেট ছিল। ১২ বছরে মেট্রিকুলেশন, ১৪ তে কলকাতার কলেজ থেকে আইএসসি এবং ১৬ তে কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্সে একাধারে অনার্স এবং বিএসসি পাশ করেন। এরপর বাবার চাপে বেদ, উপনিষদ, আয়ুর্বেদ নিয়ে পড়াশোনা করেন। এরপর কলকাতার স্কটিশ চার্চে প্রোফেসর হিসেবে নিযুক্ত হন।
প্রোফেসর শঙ্কু ছিলেন তুখোড় জ্ঞানী। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করতেন না তবে ভূত-প্রেত এ বিশ্বাস করতেন। তার প্রপিতামহ বটুকেশ্বরের সাথে 'প্রফেসর শঙ্কু ও ভূত' গল্পে পরিচয় ঘটে৷ গিরিডিতে চাকর প্রহ্লাদ ও বিড়াল নিউটন যার বয়স ২৪ বছর তাদের নিয়েই থাকেন তিনি। প্রখ্যাত সব বিজ্ঞানীদের সাথে তার উঠবস। তন্মধ্যে দুটো নাম বেশি এসেছে তারা হলো জার্মান নৃতত্ত্ববিদ উইলহেম ক্রোল এবং ব্রিটিশ ভূতত্ত্ববিদ জেরেমি স্যান্ডার্সের নাম। এছাড়াও প্রতিবেশী অবিনাশ চট্টোপাধ্যায় ও হিতাকাঙ্ক্ষী নকুড়বাবু ছিল তার কাছের বন্ধু।
সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ হচ্ছেন প্রোফেসর শঙ্কু। টাক মাথা, অকুতোভয়, আত্মভোলা, অসীম প্রতিভার বিজ্ঞানী হলেন শঙ্কু। শঙ্কুর বয়স সম্পর্কে কিছুটা দ্বিমত থাকলেও অধিকাংশ মনে করেন ১৯১২ কিংবা ১১ সালে তার জন্ম। ঠিক সে সময় স্যার আর্থারের রচনায় বেরিয়েছিল প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের দুর্ধর্ষ এক কাহিনি। এ নিয়ে সত্যজিৎ লেখেন, "শঙ্কু আসলে, mild-mannered version of Professor Challenger."
একটু পড়লেই বুঝতে পারবেন কেন সত্যজিৎ এ কথা বলেছিলেন। প্রোফেসর চ্যালেঞ্জার ছিলেন ভীষণ রাগী অন্যদিকে প্রোফেসর শঙ্কুর প্রথম গল্প ব্যোমযাত্রীর ডায়েরিতেও পাওয়া যায় তিনি অত্যন্ত বদরাগী একজন মানুষ। যে কি না চাকর প্রহ্লাদকে একটু ভুল হলেই ভীষণ বকাঝকা করেন। এমনকি নিজের আবিষ্কৃত স্নাফ গান প্রহ্লাদের গোঁফের কাছে প্রয়োগ করেছিলেন একবার।
এছাড়াও আরও কিছু জায়গায় তার রাগ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী গল্পে এর বিস্তর ফারাক দেখা গিয়েছিল বলতে গেলে।
প্রোফেসর শঙ্কুর আবিষ্কারও ছিল বেশ চমকপ্রদ। প্রোফেসর শঙ্কু আবিষ্কৃত ‘অ্যানাইহিলিন পিস্তল’ এমন একটি অস্ত্র যা লক্ষ্য স্থির করে চালালেই লক্ষ্যবস্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়! ‘স্বর্ণপর্ণী’ গল্পে শঙ্কু তাঁর ডায়রিতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আমার অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ জীবনে আমাকে অনেকবারই চরম সংকটে পড়তে হয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য একটা অস্ত্রের প্রয়োজন, অথচ আমি রক্তপাত সহ্য করতে পারি না। তাই এই পিস্তল, যা শত্রুকে নিহত না করে নিশ্চিহ্ন করে।"
প্রোফেসর শঙ্কুর আরেকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি ‘কার্বোথিন বস্ত্র’। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘প্রোফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল’ গল্পে শঙ্কু তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন, "সেবার গিরিডিতে ঝড়ের মধ্যে আমার বাগানের গাছের চারাগুলো বাঁচাতে গিয়ে কাছাকাছি একটা তালগাছে বাজ পড়ায় আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরেই এই জামাটা আবিষ্কার করি এবং ২৪ ঘন্টা পরে থাকি।" কার্বোথিন বস্ত্র বিদ্যুৎ অপরিবাহী, তাই এর দ্বারা তৈরী জামা বৈদ্যুতিক শক থেকে সুরক্ষিত রাখে। সেই গল্পে নরওয়েজীয় শিল্পী গ্রেগর লিন্ডকুইস্টের একটি অদ্ভুত ও নির্মম শখ ছিল। একটি ইলেকট্রনিক মেশিনের সাহায্যে বিশ্ব বিখ্যাত মানুষদের তিনি ছ’ইঞ্চি লম্বা জ্যান্ত পুতুলে রূপান্তরিত করতেন। শঙ্কুরও সেই হাল করতে চেয়েছিলেন তিনি। গেঞ্জির নীচে পরা কার্বোথিনের পাতলা জামাটা সেদিন তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।
এছাড়াও স্নাফ গানও আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। আবিষ্কার করেছিলেন দুটো রোবট। একটার নাম ছিল বিধুশেখর আর আরেকটার নাম ছিল রোবু। ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি গল্পে প্রোফেসর শঙ্কু বিধুশেখরকে নিয়ে মঙ্গলেও গিয়েছিলেন।
গিরিডি শহরের স্থায়ী বাসিন্দা প্রোফেসর শঙ্কু কর্মসূত্রে পৌঁছে গিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জার্মানি, নরওয়ে, সুইডেন, তিব্বত, জাপান, স্পেন, মিশর, বলিভিয়া, ইরাক সহ পৃথিবীর নানান দেশে আর জড়িয়ে পড়েছেন বিস্ময়কর সব অভিযানে। প্রোফেসর শঙ্কুর গল্পে শুধু বিজ্ঞানই ছিল না। ছিল ভৌতিক এক্সপেরিমেন্টও। প্রোফেসর শঙ্কু ও ভূত গল্পে এর দারুণ মিশেল পাওয়া যায়। তথা বিজ্ঞান এবং ভৌতিক বিষয়বস্তুর এক দারুণ মেলবন্ধন করাতেন শঙ্কু।
তাড়িনীখুড়ো:
ফেলুদা এবং প্রোফেসর শঙ্কুর পরে সত্যজিৎ সৃষ্টি করেন তাড়িনীখুড়ো চরিত্রটাকে। এই চরিত্রের ভূমিকাই ছিল গল্প বলা। তথা সত্যজিৎ চেয়েছিলেন একজন মানুষ তার জীবনের সবরকম গল্প সবার কাছে বলে বেড়াবে। আর এর জন্যই তিনি সৃষ্টি করেন তাড়িনীখুড়োকে।
তাড়িনীখুড়ো চরিত্রের মূল নাম তাড়িনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার বসবাস কলতার কলেজ স্ট্রিটের বেনিয়াটোলা লেনে। পাঁচজন ছেলেকে তার জীবনের সব চড়াই উৎরাইয়ের গল্প বলাই তার অন্যতম কাজ। তার গল্পগুলো একাধারে ভৌতিক আবার হাসির ছিল। তবে তার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের বিকাশও ছিল। তার গল্পগুলো ছিল অনেকটা তার জীবনে ঘটে যাওয়া লোমহর্ষক কাহিনি এবং সেখানে ভাগ্য আর বুদ্ধির জোরে সে কীভাবে বেঁচে ফিরেছিল তার উদাহরণ।
তিনি সারা ভারতের তেত্রিশটা শহরে ঘুরে ছাপ্পান্ন রকমের চাকুরি করেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি গল্প বলেন।
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অবিবাহিত। প্রশ্ন আসতে পারে তবে পাঁচ ছেলে হলো কীভাবে?
এর উত্তর হলো সেই পাঁচজন ছেলে তাড়িনীর না। তাড়িনীখুড়োর গল্প পড়লে দেখবেন যে সেখানে গল্প বলছে পল্টু। তাড়িনীখুড়ো পল্টুদের বাড়িতে ঘন ঘন যাওয়ার ফলে পল্টু তাকে খুড়ো বলেই ডাকতে শুরু করে৷ আর এর দরুন পল্টুর চার বন্ধুও তাকে খুড়ো বলে ডাকে।
তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তেমন জানা যায় না। তিনি সবার খুড়ো। বরঞ্চ খুড়ো না বললেই তিনি চটে যান। যদ্দুর জানা যায় তিনি মাঝারি গড়নের ছিলেন। কানের ওপরে কিছু চুল ছিল। আদি বাসস্থান ঢাকায় হলেও ভারতেই থাকেন। কলকাতার স্ট্রিট রোডে বয়স ৬৪তে গিয়ে থিতু হয়েছিলেন।
নাম না থাকা চরিত্র:
১৯৭০ সালের দিকে ছাপার খরচ বেড়ে যাওয়ায় সন্দেশ পত্রিকা মাসিক থেকে দ্বিমাসিক হয়ে যায়। পাতাও কমে যায় অনেক। তবে ভালোর মধ্যে থাকে কাগজের আকৃতি বেড়ে যাওয়া। যার দরুন প্রচ্ছদের জন্য বেশ কিছু জায়গা পান সত্যজিৎ রায়। আর এই বিষয়টাকেই কেন্দ্র করে গড়েন এক চরিত্র। সত্যজিৎ কমিকস্ট্রিপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন একটা চরিত্র। সেই চরিত্রের কোনো নাম নেই। মূলত কোনো নাম তো দূর কোনোরকমের সংলাপই সেই চরিত্রের নেই। তবু সে সময় কমিকটা বেশ সাড়া ফেলে।
আমরা অনেকেই জানি সত্যজিৎ ছবি আঁকায় ওস্তাদ। তার চেয়েও বড়ো বিষয় তিনি কমিক বেশ পছন্দ করতেন। টিনটিন এর প্রথমদিককার একজন ভক্ত ছিলেন সত্যজিৎ। আর এর জন্যই শিশুদের জন্য তৈরি করেন এক কমিক চরিত্র।
দ্বিমাসিক সন্দেশের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ পায় দীপক চক্রবর্তীর কমিকস। এর পরেই কলম তুলে নেন সত্যজিৎ। সৃষ্টি করেন জীবনের প্রথম কমিকস।
কমিকসের চরিত্রটি একটি ছাপোষা বাঙালির ন্যায়। কোঁচা করে পরা ধুতি, হাতের ছড়ি আর চুলের ভাঁজে তার বাঙালিয়ানা স্পষ্ট। চার পর্বের একটাতেও কোনো সংলাপ নেই, নেই কোনো বর্ণনাত্মক বাবলও, যা কিছু বলার সব ছবি দিয়েই বলেছেন সত্যজিৎ। আর এই মাধ্যমটার নাম দিয়েছিলেন 'ছবিতে গল্প'।
প্রখ্যাত ইলাস্ট্রেটর দেবাশীষ দেব একটা বিষয় খোলাসা করে দিয়েছিলেন। সন্দেশ তখন প্রত্যেক ঋতুতে প্রকাশ হওয়া শুরু হয়। ছয় ঋতুতে ছয়টা সংখ্যা প্রকাশ করা শুরু করে। আর সত্যজিৎ তাঁর সেই কমিকটাকে চারটা ঋতুর মধ্যে ফেলে দেন। আর কমিকের সবচেয়ে মজার বিষয় ছিল সম্ভবত এটিই।
প্রথমটা বর্ষায় ছাপা হয়। আর সেই অনুযায়ী কমিকের চিত্রেও ফুটে ওঠে বর্ষার ছাপ। পরের সংখ্যায় শারদীয় বাজির বিষয়ও ফুটিয়ে তুলেছিলেন সত্যজিৎ। তৃতীয় সংখ্যায় হেমন্তকালের দৃশ্য দেখা যায় তথা পরীক্ষার পরে ছুটির আমেজ আর তাই এই সংখ্যায় থাকে চিড়িয়াখানার কাহিনি। আর সর্বশেষ সংখ্যায় আসে সার্কাসে কাহিনি। কলকাতায় জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে বড়ো করে সার্কাসের আসর জমে। আর এই সংখ্যায়ই সেটার দেখা মেলে। আর তার সাথে জানা যায় কমিকের মূল নায়ক একজন ট্রাপিজ। এবং তার তিনটে ছেলেমেয়েও আছে।
দুঃখের বিষয় এই যে বড়ো সংখ্যার সন্দেশ আরও বছর তিনেক চললেও সেই কমিকের আর কোনো দেখা মেলেনি। চার পর্বেই সমাপ্ত করে দেন সত্যজিৎ কমিকটাকে। হয়তো ছোটোদের জন্য কমিকটি বেশিই কঠিন হয়ে যাচ্ছিল তাই সমাপ্তি টেনে ছিলেন তিনি।
সাহিত্যজগতে সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্ট সকল চরিত্র টানা অসম্ভব। প্রত্যেকটা গল্পেই বিভিন্ন চরিত্র ছিল। তবে যে চরিত্রগুলো একের অধিক এসেছিল বা টার্নিং পয়েন্টে ছিল তাদের নিয়েই আলোচনা করেছি। তা-ও বেশ বড়ো ধরনের একটা আর্টিকেল হয়ে গেছে। অনেক কিছুই এড়িয়ে গিয়েছি শব্দের ব্যপ্তি দেখে।
লেখা: বি. এম. পারভেজ রানা (লেখক ও অনুবাদক)
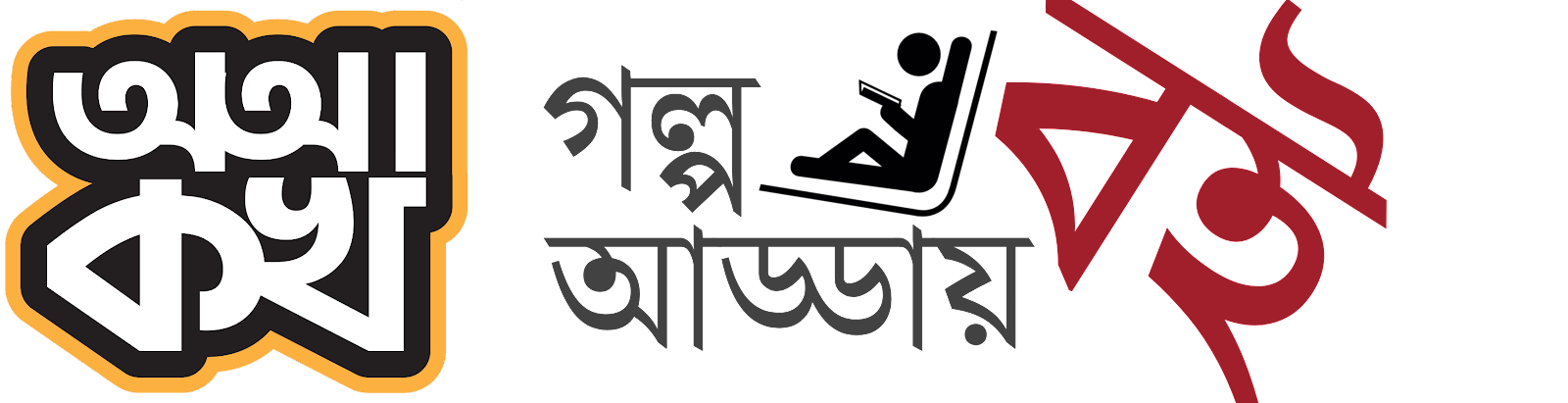

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)