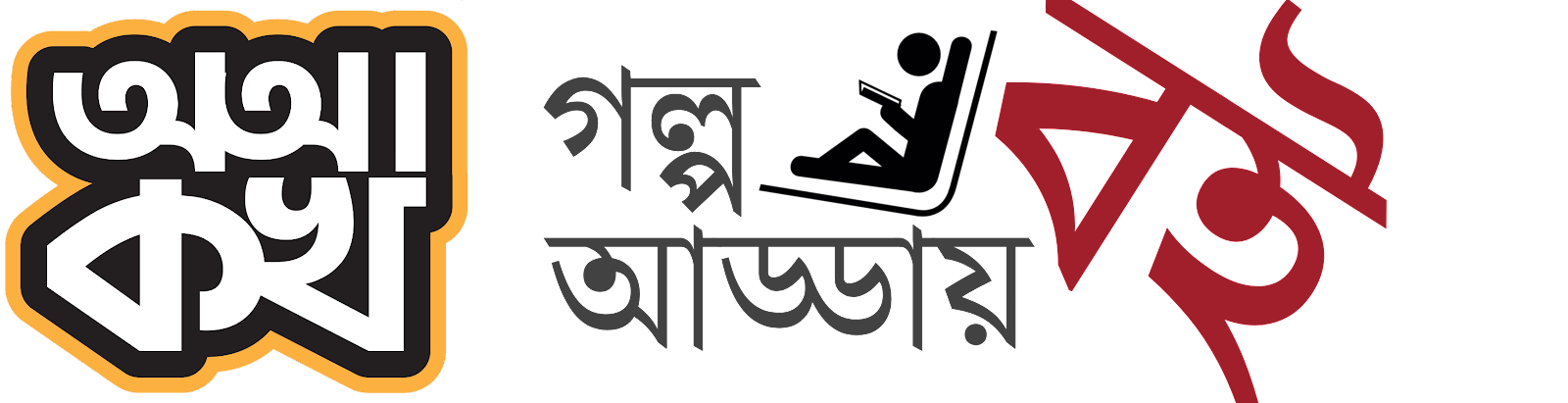"মনের মন্দিরে: স্মৃতির পরম্পরায়"
স্মৃতিকথা কিংবা আত্মচরিতগুলো সমাজ ও সংস্কৃতিচিন্তার বিরাট আকর। বাংলা অঞ্চলে সাহিত্যকেন্দ্রিক পাঠাভ্যাস কীভাবে গড়ে উঠেছিল তার হদিস মেলে এ জাতীয় গ্রন্থগুলোতে৷ হোক তা কোনো কবি-লেখকের স্মৃতি বা জীবনচরিত, কিংবা অখ্যাত কোনো সাধারণের ব্যক্তিচরিত। জীবনের আদি-মধ্য-অন্ত্যের ছোট ছোট সঙ্গমে মিলে যায় সাহিত্যের বইপুস্তক পড়ার নজির। বাংলা অঞ্চলে বিকশিত 'লিটারেরি কালচার' বা 'সাহিতাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি'র আদ্যোপান্ত খুঁজে দেখা যেতে পারে পূর্ববঙ্গীয় জনপদের মানুষের স্মৃতিপরম্পরায়। দেখতে পাই, সেই সব বয়ানলেখায় মধুসূদনও হাজির। যেমন, মেঘনাদবধ কাব্যের প্যারডি ছুছুন্দরীবধ কাব্যের রচয়িতা জগদ্বন্ধু ভদ্র ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেনের সাক্ষাৎ শিক্ষক। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য (১৯২২) বইয়ে তাঁর উল্লেখ আছে। জসীম উদদীনের জীবনকথায় (১৯৬৪) জানা যাচ্ছে তাঁর বাবার পাঠ্যতালিকা; দূর সেই কালে 'ছাত্রবৃত্তি স্কুলে'র একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে হয়েছে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্ভাবশতক, মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য, নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ। শিশু-কিশোর সাহিত্যিক ননীগোপাল চক্রবর্তী মাইকেলের মতোই যিনি একজন যশুরে এবং শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে যিনি কলকাতায় স্থিত হয়েছিলেন- তাঁর অনুসৃতি (২০১১) বইয়ে লিখেছেন, 'মাইনর স্কুলে আমাদের সীতার বনবাস, চাণক্য শ্লোক, মেঘনাদবধ কাব্য প্রভৃতি বই পড়তে হতো, কিন্তু পরীক্ষার সময় ওর থেকে কোনো প্রশ্ন আসে নি।' (পৃ. ৫২)। অনুসৃতি বইয়ের অন্য এক অংশে জানা যাচ্ছে ননীগোপালের মায়ের স্মৃতিতেও মিশে আছে মধুসূদন পাঠের অভিজ্ঞতা। এ রকম আরও কয়েকটি লেখার সাক্ষ্য মানা যাক।
আমরা বেছে নিচ্ছি এমন একজন ব্যক্তিত্বকে যিনি সাহেবি কেতায় নিজেকে গড়েপিটে তৈরি করেছিলেন: এক সময় ইংল্যান্ড হয়ে উঠেছিল তাঁর আবাসভূমি তিনি নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, পূর্ববঙ্গের কিশোরগঞ্জে তাঁর জন্ম, যদিও কখনো কখনো দাবি করেছেন যে, তাঁকে পূর্ববঙ্গীয় না বলাই ভালো। তাঁর আত্মজীবনী দ্য আটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান-এর (১৯৫১) পাতাগুলো তিনি ভরে তুলেছেন এ অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপকরণ দিয়ে। ঘরের আসবাবপত্রের নিখুঁত বর্ণনাও বাদ যায় নি তাঁর লেখা থেকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, কাচঘেরা কাপবোর্ডের এক শেলফে ছিল কিছু বই বাইবেল, ইংরেজি অভিধান, জন মিলটনের কাব্যসমগ্র, শেকসপিয়রের জুলিয়াস সিজার ও ওথেলো, কানিংহামের হিস্ট্রি অব শিখ, ওয়ারেন হেস্টিংসের অভিশংসনের ওপর বার্কের বক্তৃতা-সংকলন, বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু উপন্যাস এবং মাইকেল মধুসুদন দত্তের দুই খণ্ডের কাব্যসংগ্রহ।
মধুসূদনের নামের পূর্বভাগে নীরদ চৌধুরী লিখেছেন, 'দ্যা ফার্স্ট মডার্ন বেঙ্গলি পোয়েট'। পিতৃপুরুষের ভিটায় দেখা দুর্গাপূজার স্মৃতিচিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি চলে গেছেন মধুসূদনের সাহিত্যে। কেননা তাঁর গ্রামের প্রাচীন কবিরা যেমন করে নবমীর রাতে বিদায়ী ব্যথায় গান ধরতো তেমন করে মধুসূদনও লিখেছেন বিজয়া দশমীর শোকাতুর অনুভূতি। মধুসূদনের 'বিজয়া-দশমী' সনেটের একটি ইংরেজি অনুবাদ তিনি সংযোজন করেছেন এই আত্মকথায়। পূর্ববঙ্গের পটভূমিতে নীরদ চৌধুরীর মধুসূদন বিষয়ক স্মৃতি মোটা দাগে এইটুকুই। তবে আরও কিছু কথা তিনি আলাপের পরিসরে নিয়ে এসেছেন। সেখানে মধুসুদনকে তিনি স্থাপন করেছেন 'ভারতীয় রেনেসাঁ' ও 'বাঙালি মানবতাবাদে'র পটভূমে। উনিশ শতকের বাংলা ও বাঙালির মূল্যায়নে এটিই ছিল তাঁর তাত্ত্বিক অবস্থান। সেই ধারা অনুসরণে মধুসূদন প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'মধুসূদন হলেন বাঙালি মানবতাবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ও শহিদ।'
নীরদ চৌধুরীর সমকালীন এবং একই অঞ্চল ও ভৌগোলিক সীমানার বাসিন্দা আবুল মনসুর আহমদ যিনি কবি নন, কথাসাহিত্যিক ও রাজনীতিক। তাঁর আত্মকথায় বিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সাহিত্য ও বইকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সূক্ষ্ম অবয়ব খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রামী ও শহরে পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য অধ্যয়ন ও লিখনের ধরনগুলো এখানে বেশ স্পষ্ট। আত্মকথায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রসঙ্গে অনেকগুলো পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন আবুল মনসুর আহমদ। কিশোর অথবা এক অনতি-তরুণের বয়ানে উঠে এসেছে মাইকেলের পরিগ্রহণের প্রতিচ্ছবি। আবুল মনসুর আহমদের মধ্যে জাতীয় ও সম্প্রদায়গত চিন্তা তখনও কেন্দ্রীভূত হয় নি। তিনি মধুসুদনের কাব্যপাঠ, পুস্তকক্রয়, এমনকি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বৃত্তান্তও লিখে গেছেন। আত্মকথার এই অংশের নাম দিয়েছেন 'মাইকেলের প্রভাব'।
আবুল মনসুর আহমদের স্মৃতি-বিবরণে জানা যাচ্ছে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে মেঘনাদবধ কাব্যের ছোট্ট একটি অংশ ছিল- 'একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে'। এরপর পুরো মেঘনাদবধ কাব্যই তিনি পড়ে ফেলেছিলেন, সঙ্গে ছিল পলাশীর যুদ্ধ, বৃত্রসংহার ও মহাশশ্মশান। নবীনচন্দ্র ও কায়কোবাদকে তাঁর মনে হয়েছিল অনেক সহজ। অন্যদিকে, মাইকেলের কবিতাকে মনে হয়েছিল 'অনেক কঠিন'। কঠিন বলেই যেন মনে হয়েছিল 'শ্রেষ্ঠতর কাব্য'। কবিতা সম্পর্কে তাঁর এমন বোধ গড়ে উঠেছিল যে, কঠিন শব্দ আর দুর্বোধ্যতাই উৎকৃষ্ট কবিতার নির্ণায়ক। পাঠক বারবার অভিধান দেখবেন, গলদঘর্ম হয়ে শব্দার্থ খুঁজবেন, এখানেও নিহিত কবির অক্ষয় কৃতিত্ব। মধুসূদনের প্রভাবে সরল স্বীকারোক্তি করেছেন আবুল মনসুর আহমদ, 'আমি অমিত্রাক্ষর ছন্দে যথাসম্ভব দুর্বোধ্য কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম। (পৃ. ২৬১)।
কবিতা নিয়ে হাত মকশো করার স্মৃতি আওড়াতে গিয়ে মনসুর আহমদ লিখেছেন, যখন গ্রামে ছিলেন তখন পুঁথি-কবিতায় ব্যবহৃত ছন্দের অনুসরণ করতেন। সেগুলো ছিল মিত্রাক্ষর এবং আকারপ্রকারে ছিল পয়ার, ত্রিপদী, একাবলি ইত্যাদি। কিন্তু ময়মনসিংহ শহরে যাওয়ার পর মাইকেল, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও কায়কোবাদের বই পড়ে লিখতে শুরু করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে। এক্ষেত্রেও মনসুর আহমদ ঠাট্টার ছলে লিখেছেন, 'আমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখিবার নিয়ম প্রচলন করায় মাইকেল ও তাঁর অনুসারী কবিদের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। কারণ পয়ার, ত্রিপদীর চেয়ে মিলহীন কবিতা লেখা অনেক সোজা বলিয়াই ছিল তৎকালে আমার বিশ্বাস।' (পৃ. ২৫৯)। মজার একটি সাংস্কৃতিক সাবটেক্সট লক্ষ্যযোগ্য, তা হলো, আবুল মনসুর আহমদের স্মৃতিতে গ্রামীণ পুঁথি মানেই মিত্রাক্ষর, শহর মাত্রই অমিত্রাক্ষর। গ্রামীণ পাঠক শহরে গিয়ে পেয়ে গেছে নতুন রুচির ভাষা ও সাহিত্য। তথ্য হিসেবে জরুরি আরেকটি কথা লিখেছেন আবুল মনসুর আহমদ, 'মাইকেলের মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আমরা কেউ ডা. আবুল হোসেনের যজমভগ্নি কাব্যও কিনিয়াছিলাম।' (পৃ. ২৫৮) বোঝা যাচ্ছে, সাহিত্যের সম্প্রদায়গত পরিচয়ও প্রভাবিত করেছিল তরুণ মধুসুদন- পাঠককে।
বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি। নোয়াখালী শহরের জলহাওয়া আর মেঘনা নদীর অনন্ত কল্লোলে দিন কাটছে এক কিশোরের, যে কিশোর আকণ্ঠ ডুবে আছে ইংরেজি ভাষা ও কবিতায়, সেই কিশোরের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে মধুসূদন, হেম, নবীনের। সেই কিশোর এক কালে হয়ে উঠেছেন রবীন্দ্র-উত্তর কবিতার পুরোধা, পশ্চিমী আধুনিকতার প্রচারক তিনি বুদ্ধদেব বসু। আমার ছেলেবেলা বইয়ে পাওয়া যাচ্ছে বুদ্ধদেবের মধুসূদন-সংলগ্নতার একটি ছবি। কিশোর বুদ্ধদেব ও বন্ধুরা মিলে একটি নাট্যদল গড়ে তুলেছিলেন: ছন্দের মোহনীয় টানে তাঁরা মধ্যে হাজির করেছিলেন মেঘনাদবধ কাব্যের 'সংকলিত দৃশ্য' সেই দৃশ্যমালার অভিনয় দেখে বাহবা দিয়েছিলেন শহরে প্রতিবেশীজন। অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, নোয়াখালী শহরের ছোট্ট কিশোরের দল মেঘনাদবর কাব্যের নাট্য-সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন, যা একালে বাস্তবায়িত হয়েছে কলকাতায়। আমার ছেলেবেলায় মধুসূদন দত্তকে পাওয়ার বৃত্তান্ত যেমন আমরা পাই, তেমনি পেয়ে যাই তাঁকে হারিয়ে ফেলার গল্প। বুদ্ধদেব বসু যখন পরিচিত হলেন রবীন্দ্র-কবিতার সংকলন চয়নিকার সঙ্গে, মগ্নভাবে প্রবেশ করলেন রবীন্দ্রজগতে তখন দূরবর্তী রেখার মতো মিলিয়ে গেল মধুসূদন, হেম, নবীনের জগৎ।
সুন্দর একটি স্মৃতির মুখোমুখি করেছেন কবি, অনুবাদক ও ঔপন্যাসিক মনিরউদ্দীন ইউসুফ যাঁকে আমরা প্রধানত শাহনামার অনুবাদক হিসেবে চিনি। তাঁর আমার জীবন আমার আভিজ্ঞতা বইয়ে উঠে এসে মধুসূদন পাঠের স্মৃতি। তাঁর পরিবারে আরবি, ফারসি ও উর্দুর কদর ছিল; এই ভাষাগুলোর বনেদি ইতিহাস তার প্রধান কারণ। কিন্তু কিশোর এই কবির মর্মজুড়ে দখল করে নিয়েছিল বাংলা। বাংলা বইয়ের সূত্র ধরে এসেছিলেন মধুসূদন। তারই মাঝখানের এক টুকরো গল্প:
তখন ক্লাস সিকসে পড়ি। ক্লাসের দক্ষিণমুখী জানালাগুলির পথে দিগন্তপ্রসারিত জলরাশি দেখা যায়। সৈয়দ শামসুদ্দীন নামে নর্মাল পাস পণ্ডিত সাহেব আমাদের পড়াচ্ছেন, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্য থেকে 'অশোক বনে সীতা' অংশটি। সুন্দর কন্ঠের সেই আবৃত্তি এখনও তুলতে পারি না।... সীতা যেন আমাদেরই পরিবারের কোন সুন্দরী ধৈর্যশীলা মহিলা। তাঁর দুঃখে আমি দুঃখিত। দক্ষিণের বারিত্রাশির উপর দিয়ে সে মুখে যেন দূবের কালো রেখাটায় গিয়ে মিশেছে।
কি যে, অনুভূতি, কি উপলব্ধি। মনে হতো আমি যেন সেইক্ষণে মাইকেলের ইন্দ্রিয়গুলোকে ছুঁয়ে চলেছি। কোন প্রাচীনকালের সীতা যেন আমার মা-খালার মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠছেন। (পৃ. ৩১)
অনুরাগ ও অনুভবে মেশা ব্যক্তিক এই পাঠ মর্মস্পর্শী। স্মৃতির কুয়াশায় ভাসতে ভাসতে পাঠক হিসেবে আমরা চলে যাই শহর থেকে দূরে জলপ্লাবনে ভাসা এক স্কুলের ক্লাসরুমে কিশোর এক শিক্ষার্থী সীতাকে গ্রহণ করেছে পরিজনের অন্দরমহলে। মনিরউদ্দীন ইউসুফ যখন শোকাতুর বিষাদে নিমজ্জিত, কাছাকাছি বয়সের এক কিশোরী তখন ভাবছেন মাইকেলের কবিতার ছন্দ নিয়ে, 'এ কেমন কবিতা? এ কেমন ছন্দ?' পরবর্তী জীবনে এই প্রশ্নের জবাবগুলো সে খুঁজেছিল বিদ্যায়তনিক পরিসরে
নীলিমা ইব্রাহিম নামে, বাংলার কবি মধুসূদন বইয়ে। এই বইয়ের ভূমিকা অংশে ভেসে উঠেছে কিশোরী নীলিমার মধুসূদন-স্মৃতিঃ বাবার চুল আচড়ানোর ধরন দেখে তাঁর কৌতুহলী মন জানতে চেয়েছিল, বাবা কেন মাঝখানে সিঁথি করেন। বাবা তখন মাইকেলের ছবি বের করে দেখিয়েছিলেন, স্টাইল করা এই প্রিয়ভাজনের অনুকরণেই তিনি চুল আচড়ান এবং শুনিয়েছিলেন মাইকেলের 'নাটকীয় জীবনকাহিনী'। নীলিমা লিখেছেন, 'ঔৎসুক্য বেড়ে চলল কবি সম্পর্কে। প্রায়ই প্রশ্ন করতাম বাবাকে আর শুনতাম তাঁর কাব্য কাহিনী।' একবার তাঁদের বাড়িতে এলেন বাবার বন্ধু শিশির কুমার ভাদুড়ী। তাঁর কণ্ঠে শোনা হলো মধুসূদনের কবিতা। ওই পর্বে তিনটি দিন ধরে গভীরভাবে চলল মধুসূদনের কাব্যপাঠ ও প্রশস্তি। ঘটনার তুমুল তন্ময়তায় নীলিমার সামনে খুলে গেল 'মধুকাব্যের সিংহদ্বার।' এ কালের পাঠকের কাছে বিস্ময়কর মনে হলেও এটাই সত্যি যে, সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসেবে সাহিত্যের প্রভাব এমন তীব্র ও তীক্ষ্ণই ছিল।
মজার একটি কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। ঘটনাটি তাঁর কিশোর বয়সের। পুরনো প্রবাসী পত্রিকার পাতা ঘেঁটে নিজের নামে মাইকেলের একটি কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রঙধনু নামের অন্য এক পত্রিকায়। নিজের লেখা কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে না দেখে অপেক্ষায় ক্লান্ত হতে হতে গুণ এই 'দুষ্টুবুদ্ধি'র প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। তবে রঙধনুর সম্পাদক সেটি ধরতে পেরে গুণকে ফিরতি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তুমি রঙধনুতে ছাপার জন্য যে কবিতাটি পাঠিয়েছ, তা মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা। তুমি নিজের লেখা কবিতা পাঠাও। অন্যের লেখা কবিতা আর পাঠাবে না।' (পৃ. ৭২) কিশোর-কবি নির্মলেন্দু গুণের ভাবনাটি ছিল এ রকম, 'উনি যে ঐ মাইকেল মধুসূদন তা তখন আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম, অন্য কোনো মধুসূদন হবে। বাংলা সাহিত্যে যে মধুসূদনের এমন আকাল, তা কে জানত?' (পৃ. ৭২) গুণের এই গল্প আছে তাঁর মহাজীবনের কাব্য বইয়ে। পরিণত বয়সের স্মৃতিলেখায় নির্মলেন্দু গুণ পরিহাস করেছেন ঠিকই, কিন্তু সংকেতময় একটি বার্তাও দিয়েছেন, তা হলো, বাংলা সাহিত্যে 'মধুসুদনের এমন আকাল'। অর্থাৎ সাহিত্যের বিচিত্র নিরীক্ষা নিয়ে দশকে দশকে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন আসেন নিঃ মধুসূদনের আমূল প্রভাববিস্তারী প্রতিভার দিকেই নির্মলেন্দু গুণের এই কড়ানাড়া।
* প্রবন্ধটির সাতটি অংশ, সাতটি পর্বে প্রকাশিত হবে। আজ প্রথম পর্ব মনের মন্দিরে স্মৃতির পরম্পরায় প্রকাশ করা হলো।